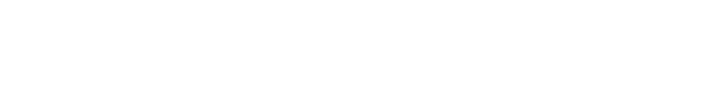গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩ জুলাই-২০২৫ এ প্রকাশিত ‘জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি’ বিষয়ক পরিপত্রটি দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ২০% এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০% নবায়নযোগ্য উৎস থেকে পূরণের যে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য সরকার নির্ধারণ করেছে, এই কর্মসূচি তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমানে সৌর বিদ্যুৎ থেকে মাত্র ৫.৬% বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে, যা প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। এই প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক গ্যাসের দ্রুত ফুরিয়ে আসা মজুদ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার তাগিদ থেকে এই কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। তবে, এই মহৎ উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

কর্মসূচির মূল দিক এবং লক্ষ্যমাত্রা:
পরিপত্র অনুযায়ী, এই কর্মসূচির দুটি প্রধান কৌশলগত দিক রয়েছে:
- উদ্যোগ ‘ক’ (সরকারি অফিস): সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবনের ছাদে (ভাড়া করা স্থাপনা ব্যতীত) সোলার প্যানেল স্থাপন করা হবে CAPEX (Capital Expenditure) মডেলে। এর জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ছাদের আয়তন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বিবরণ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় জানা যাবে। নেট মিটারিং পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ বিল সমন্বয় করা হবে।
- উদ্যোগ ‘খ’ (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য স্থাপনা): স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও হাসপাতালে OPEX (Operational Expenditure) মডেলে বিনিয়োগ করা হবে, যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনও ব্যয় বহন করতে হবে না। এতে তাদের বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে।
লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যে, ডিসেম্বর ২০২৫ সালের মধ্যে এই কর্মসূচির আওতায় দেশের জাতীয় গ্রিডে প্রায় ৩,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযুক্ত করা হবে। এটি বার্ষিক ৪,২০০ কোটি টাকা অর্থসাশ্রয় করবে, ২৫,২০০ কোটি টাকার আর্থিক মূল্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, ১৮ লক্ষ টন জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাবে এবং ২৫ লক্ষ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ হ্রাস করবে। এছাড়াও, কার্বন ক্রেডিট বিক্রির মাধ্যমে বছরে প্রায় ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এবং ১,০০,০০০ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রত্যাশা করা হয়েছে।
CAPEX মডেলের উপযুক্ততা এবং চ্যালেঞ্জ:
পরিপত্রে সরকারি অফিসগুলোতে CAPEX মডেলে সোলার সিস্টেম স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এই মডেল অনুযায়ী, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব অর্থায়নে সোলার প্যানেল স্থাপন করবে। যদিও এটি দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ে সহায়ক হতে পারে, তবে এর সফল বাস্তবায়নে বেশ কিছু গুরুতর চ্যালেঞ্জ রয়েছে।
প্রথমত, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব:
অধিকাংশ সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কারিগরি দিক, রক্ষণাবেক্ষণ, এবং সর্বোত্তম কার্যকারিতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। CAPEX মডেলে সিস্টেম স্থাপনের পর এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমস্যা সমাধানে তারা হয়তো সক্ষম হবেন না। ফলে, মূল্যবান সরকারি অর্থ ব্যয় করে স্থাপিত সোলার সিস্টেমগুলো অদূর ভবিষ্যতে অব্যবহৃত স্ক্র্যাপে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। একটি সোলার সিস্টেমের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, এবং ত্রুটি মেরামতের প্রয়োজন হয়, যা সরকারি দপ্তরগুলোর নিয়মিত কাজের অংশ নয়।
দ্বিতীয়ত, প্রচুর সরকারি অর্থের প্রয়োজন এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা:
CAPEX মডেলের জন্য বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের প্রয়োজন হবে। এই অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যয়ের প্রক্রিয়াটি আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হতে পারে। অর্থ বিভাগ থেকে বরাদ্দ গ্রহণ, দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন এবং কার্যাদেশ প্রদান- এই প্রতিটি ধাপে আন্তঃমন্ত্রণালয় চিঠি চালাচালি এবং অনুমোদনের প্রয়োজন হবে, যা পুরো প্রক্রিয়াটিকে বিলম্বিত করতে পারে। পরিপত্রে ৩-৬ মাসের মধ্যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলা হলেও, বাস্তবক্ষেত্রে এটি আরও বেশি সময় নিতে পারে, যা ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৩,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
OPEX মডেলের কার্যকারিতা এবং এর চ্যালেঞ্জ:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য স্থাপনায় OPEX মডেলে সোলার সিস্টেম স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, যেখানে তৃতীয় পক্ষ বিনিয়োগ করবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো ব্যয় বহন করতে হবে না। এই মডেলটি তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, কারণ এখানে বিশেষজ্ঞ তৃতীয় পক্ষ লাভজনকতার উদ্দেশ্যে সিস্টেমের স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি জ্ঞান বা রক্ষণাবেক্ষণের ঝক্কি পোহাতে হবে না এবং বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে।

তবে, OPEX মডেলের সফলতার জন্যও কিছু বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন:
- PPA (Power Purchase Agreement) এবং কারিগরি বোঝাপড়ার অভাব: যদিও নেট মিটারিং সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল সমন্বয় করা হবে, তবে এর জন্য RESCO কোম্পানির সাথে একটি PPA বা সমজাতীয় চুক্তি প্রয়োজন হতে পারে। এই চুক্তি এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয়গুলো বোঝার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞান থাকা জরুরি। সঠিক কারিগরি বোঝাপড়ার অভাবে সিস্টেমের কার্যকারিতা ব্যাহত হতে পারে এবং সরকারের উদ্দেশ্য পূরণ নাও হতে পারে।
- তৃতীয় পক্ষের নির্বাচন ও তদারকি: সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তৃতীয় পক্ষ নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। PPA চুক্তি এবং কর্মক্ষমতা সংক্রান্ত শর্তাবলী সুস্পষ্ট হতে হবে এবং তা কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে।
- দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির জটিলতা: দীর্ঘমেয়াদী PPA চুক্তি প্রণয়ন এবং তার শর্তাবলী উভয় পক্ষের জন্য ন্যায্য ও টেকসই হওয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- নেট মিটারিং এর সঠিক বাস্তবায়ন: নেট মিটারিং সিস্টেমের সঠিক এবং সময়োপযোগী বিল সমন্বয় নিশ্চিত করা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। প্রতি তিন মাস অন্তর গ্রিডে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ এবং গ্রিড থেকে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ সমন্বয় করে বিল প্রদানের প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ও দক্ষ হতে হবে।
SREDA-এর ভূমিকা এবং জ্ঞান বিতরণ:
এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে স্রেডা (Sustainable and Renewable Energy Development Authority) একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। স্রেডা নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং তাদের কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এই কর্মসূচির জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।
- জ্ঞান বিতরণ ও প্রশিক্ষণ: স্রেডা সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, এর স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, নেট মিটারিং এবং PPA বিষয়ক বিস্তারিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করতে পারে।
- বুকলেট/হ্যান্ডবুক প্রণয়ন: স্রেডা একটি সহজবোধ্য বুকলেট বা হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করতে পারে, যা সাধারণ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মৌলিক বিষয়াবলী, করণীয় এবং বর্জনীয় সম্পর্কে একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। এই ধরনের একটি হ্যান্ডবুক CAPEX মডেলে স্থাপিত সিস্টেমগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করবে এবং অব্যবহৃত হয়ে পড়ার ঝুঁকি কমাবে।
- ফোকাল পয়েন্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধি: পরিপত্রে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ইউটিলিটি থেকে একজন করে ফোকাল পয়েন্ট রাখার কথা বলা হয়েছে। স্রেডা এই ফোকাল পয়েন্টদের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে, যাতে তারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ও আর্থিক বিষয়গুলো সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে সক্ষম হন।

অন্যান্য পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ:
- গুচ্ছাকারে (Bundling) ক্রয় প্রক্রিয়া: একাধিক অফিস/প্রতিষ্ঠান গুচ্ছাকারে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার যে সুযোগ রাখা হয়েছে, তা ছোট ছোট সিস্টেমের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী হতে পারে। তবে, এর জন্যও সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা এবং সমন্বয় প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন।
- ব্যাটারিবিহীন সিস্টেম: অধিকাংশ সিস্টেম ব্যাটারিবিহীন ও গ্রিডে সংযুক্ত হবে, যা সিস্টেমের খরচ কমাবে। তবে, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য স্থাপনায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট একটি বড় সমস্যা, সেখানে চাহিদার ভিত্তিতে ব্যাটারি যুক্ত করার বিষয়টি ইতিবাচক।
- হেল্প ডেস্কের কার্যকারিতা: কর্মসূচির সফলতার জন্য হেল্প ডেস্কের (সোলার হেল্প ডেস্ক, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিপিডিবি, পবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, নেসকো) কার্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই হেল্প ডেস্কগুলোকে দ্রুত ও কার্যকর সেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে।
- তদারকি ও মূল্যায়ন: কর্মসূচির নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা জরুরি। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি, সিস্টেমের কার্যকারিতা, এবং উদ্ভূত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য একটি শক্তিশালী মনিটরিং ও ইভালুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক থাকা উচিত।
- দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা: এই কর্মসূচিটি একটি ভালো সূচনা হলেও, ২০৩০ এবং ২০৪০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আরও সুদূরপ্রসারী এবং সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়োজন।
জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি” বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এটি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস, পরিবেশ সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে, CAPEX মডেলের চ্যালেঞ্জগুলো, বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কারিগরি জ্ঞান এবং অর্থায়নের দীর্ঘসূত্রিতা, সফল বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। OPEX মডেল তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর হলেও, এর সঠিক তদারকি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় স্রেডার মতো বিশেষজ্ঞ সংস্থার সক্রিয় ভূমিকা, জ্ঞান বিতরণ, প্রশিক্ষণ এবং একটি ব্যবহারিক হ্যান্ডবুক প্রণয়ন অপরিহার্য। সঠিক পরিকল্পনা, কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল, এবং নিরবচ্ছিন্ন তদারকির মাধ্যমে এই কর্মসূচি দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সত্যিই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে।